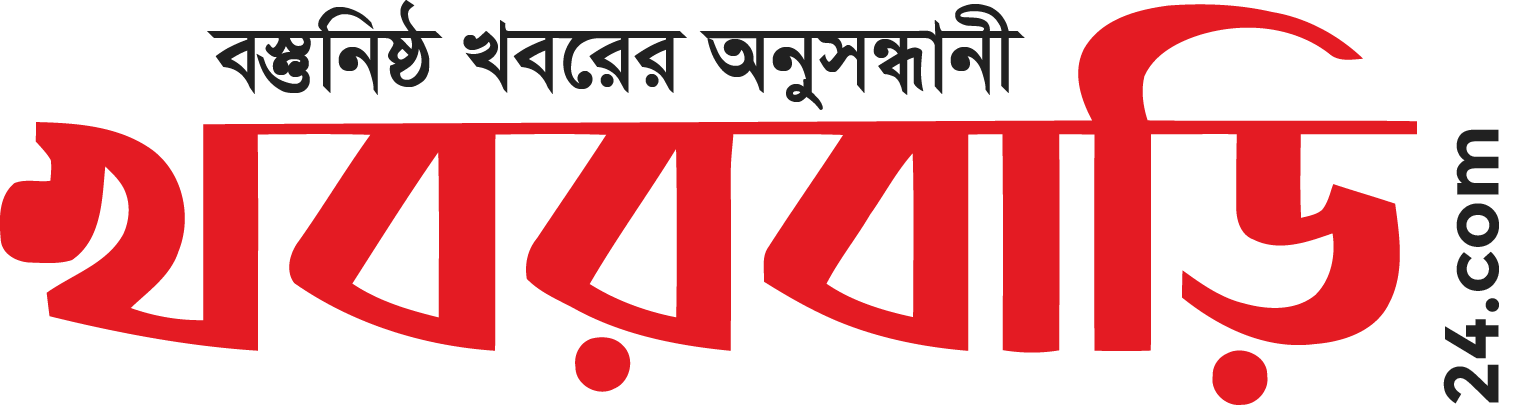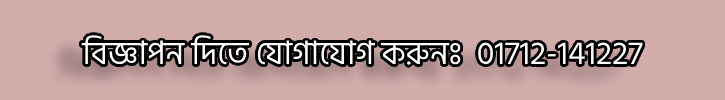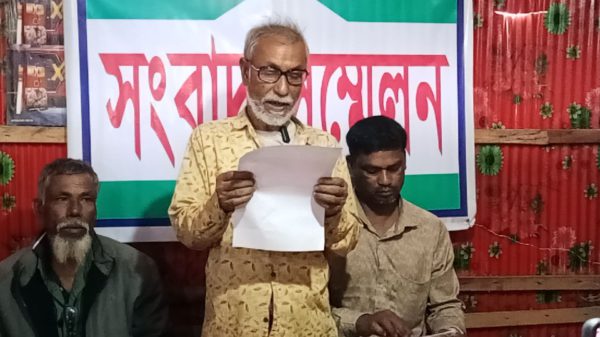ভারতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ৫০ বছর, এখনও প্রাসঙ্গিক?
- আপডেট হয়েছে : বৃহস্পতিবার, ২৫ মে, ২০১৭
- ৪১ বার পড়া হয়েছে

ভারতে ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে আজ (২৫মে ) । ১৯৬৭ সালের আজকের তারিখেই পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের কাছে নকশালবাড়ির একটি গ্রামে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন দুটি শিশু-সহ মোট এগারোজন লোক।
সেই ঘটনা থেকে যে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের সূচনা, তাতে অচিরেই যোগ দেন হাজার হাজার তরুণ – নকশালবাড়ির গন্ডী ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের নানা প্রান্তে।
নকশালবাড়ি আন্দোলন বছরকয়েকের মধ্যে স্তিমিত হয়ে এলেও অনেকেই মনে করেন আজ পঞ্চাশ বছর পরেও সেই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু হারিয়ে যায়নি।
কিন্তু অর্ধশতাব্দী পার হয়ে নকশালবাড়ি আজ ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমিতে কী তাৎপর্য বহন করে?
হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের নকশালবাড়িতে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী আজ ৫০ বছর আগের যে দিনটিকে স্মরণ করছে, তা একসময় স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিল বলে মনে করা হয়।
দার্জিলিং জেলার ওই ব্লকে জোতদার-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গরিব কৃষক ও আদিবাসীরা।
সেদিনের নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যে সিপিআই-এমএল দলটি, তার আজকের প্রধান নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর কথায়, “নকশালবাড়ি স্বাধীন ভারতের একটা টার্নিং পয়েন্ট। প্রধানত এটা ছিল কৃষক আন্দোলন, আর আজকের ভারতেও কৃষকরা কিন্তু সঙ্কটে। কিন্তু নিজেদের জীবন-জীবিকা বাঁচাতে, জমি বাঁচাতে সারা দেশ জুড়ে আজও যে কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন আমার মতে সেটা নকশালবাড়িরই ঐতিহ্য।”
“দ্বিতীয়ত সে সময় যে ধরনের ছাত্র-যুব আন্দোলন দেখা গিয়েছিল, তা প্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনীয়। হাজারে হাজারে ছাত্র গ্রামে চলে যাচ্ছেন, কৃষকের আন্দোলনে পাশে দাঁড়াচ্ছেন – এ জিনিস তো অভাবনীয় ছিল। আজকের ছাত্রদের মধ্যেও আমি সে প্রবণতা দেখি – ক্যাম্পাসে যেমন, ক্যাম্পাসের বাইরেও তেমন।”
চারু মজুমদার-কানু সান্যাল-জঙ্গল সাঁওতালদের নেতৃত্বে সেদিনের নকশালবাড়ি আন্দোলন মোটেই ব্যর্থ হয়নি বলেই তার দাবি, কিন্তু নেতৃত্বের দুর্বলতাই যে আসলে সেই আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেনি – তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই নকশাল আন্দোলনে অংশ নেওয়া ও রাষ্ট্রের জেলে চরম নির্যাতনের শিকার হওয়া জয়া মিত্রর।
“দেখুন, ভারতে বেশির ভাগ গ্রামভিত্তিক আন্দোলনের যে পরিণতি হয়, নকশালবাড়িও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মানে আমি বলতে চাইছে আন্দোলনের নেতৃত্বটা, বিশেষ করে তাত্ত্বিক নেতৃত্বটা চলে গিয়েছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। তেভাগা-তেলেঙ্গানা যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল – ঠিক একই জিনিস ঘটেছিল নকশালবাড়ির ক্ষেত্রেও।”
“যারা আন্দোলন করছেন আর শহর থেকে এসে যারা সেই আন্দোলনে যারা তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন – দুয়ের মধ্যে একটা আসলে একটা অসমানতা, বিরাট ফারাক তৈরি হয়ে গিয়েছিল”, বলছিলেন জয়া মিত্র।
কিন্তু এটা ঠিকই, যেভাবে সেদিন নিজেদের অগ্রপশ্চাৎ না-ভেবে হাজার হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন – গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বা শ্রেণীশত্রু খতম করার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে তার আর কোনও দ্বিতীয় নজির নেই।
নকশাল অন্দোলনের পটভূমিতে লেখা মাস্টারপিস ‘কালবেলা’র লেখক সমরেশ মজুমদার আবার মনে করেন ওই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অবদান পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের মানসিকতাকে চিরতরে বদলে দেওয়া।
“একাত্তরের আগে পশ্চিমবাংলার মেয়েরা পড়াশুনো করত শুধু ভাল বিয়ে হবে, এই জন্য। বাপ-ঠাকুর্দারা তাদের কলেজে পৌঁছে দিয়ে আসতেন, আবার নিয়ে আসতেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কিছু ‘বাঙাল’ মেয়েকে বাদ দিলে এই পারিবারিক অনুশাসনে বন্দি থাকাটাই ছিল তাদের রুটিন।”
“কিন্তু সাতষট্টি থেকে একাত্তর – এই চার বছর চোখের সামনে রোজ খুনোখুনি, বোমাবাজি, গুলির লড়াই দেখতে দেখতে তাদের জড়তাগুলো, মনের অন্ধকারগুলো কেটে গেল। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরাও বুঝতে শিখল, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যই তাদের পড়াশুনো করতে হবে। শুধু স্কুলেই পড়াবে না, তারা সরকারি চাকরিও করবে”, বিবিসিকে বলছিলেন সমরেশ মজুমদার।
এমন কী, আজ যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা – সাতষট্টি সালের আগে অতি বড় আশাবাদীও সে কথা কর্পনা করতে পারতেন না বলে বলছেন এই লেখক। তার মতে, এটাও নকশালবাড়ি আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার।
তবে এর পাশাপাশি সেই আন্দোলনে যে অসংখ্য তরুণের আত্মত্যাগ ছিল – ইতিহাস কি তা ব্যর্থ বলেই বিচার করবে?
লেখিকা ও অ্যাক্টিভিস্ট জয়া মিত্র একমত নন। তিনি বলছিলেন, “আজও কিন্তু মানুষ মনে রেখেছে ওই হয়তো শেষবারই বোধহয় একটা মূল্যবোধ নিয়ে ছেলেমেয়েরা লড়েছিল। গ্রাম বা মফসসলে আজও মানুষ বলেন, ওই যুবক-যুবতীরা আর যাই করুক – তারা অন্তত স্বার্থপরতা করেনি। ওরা অন্যের জন্য প্রাণ দেওয়ার, আত্মত্যাগ করার সাহস দেখিয়েছিল।”
“আমরা সে সময় অসংখ্য বীরত্বের কাহিনী দেখেছিলাম। শুধু সশস্ত্র বীরত্বেরই নয়, নি:শব্দে চরম নির্যাতন সহ্য করে যাওয়ার নীরব বীরত্বেরও”, বলছিলেন জয়া মিত্র।
আজ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে মাওবাদী বিদ্রোহের দাপট, তাদেরও অনেকে নকশালপন্থীদের উত্তরসূরী বলেই চিহ্নিত করেন। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন দুটোর মধ্যে মত ও পথের বেশ ফারাক আছে।
“আমাদের মাওবাদী বন্ধুরা যে এক ধরনের সশস্ত্র আন্দোলনের নামে, কিছু এলাকার মধ্যে আটকে আছেন তারাও কিন্তু নকশালবাড়ির ঐতিহ্য থেকে অনেকটা সরে গেছেন। খেয়াল করে দেখবেন, নকশালবাড়িতে নিশ্চয় চীন বিপ্লব বা মাও-য়ের বিরাট প্রভাব ছিল – কিন্তু তখন যে পার্টিটা গড়ে উঠেছিল তার নাম ছিল সিপিআই-মার্ক্সিস্ট লেনিনিস্ট। মাওয়ের নাম কিন্তু সেখানে ছিল না।”
“ফলে আজকের মাওবাদীদের তাদের দলের নামও পাল্টাতে হয়েছে। তারা একটা জায়গায় আটকে আছে – বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও হচ্ছে। সরকার তাদের একটা ফাঁদে ফেলে দিয়েছে, যে ফাঁদে একটা শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে”, কিছুটা হতাশার সুরেই বলছিলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।
কিন্তু ২০১৭ সালে এসেও ভারত নকশালবাড়ি আন্দোলনের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে ভুলতে পারছে তা নয়।
এ দেশে আদিবাসী-কৃষকের আন্দোলনকে ইতিহাসে নতুন করে জায়গা করে দিয়েছে, সাব-অল্টার্ন হিস্ট্রিওগ্রাফিকে নতুন করে তৈরি করেছে এবং আজও করছে শিলিগুড়ির কাছে এই ছোট্ট গ্রামটি, গবেষকরা সবাই তা মানেন প্রায় একবাক্যে।সূত্র- বিবিসি