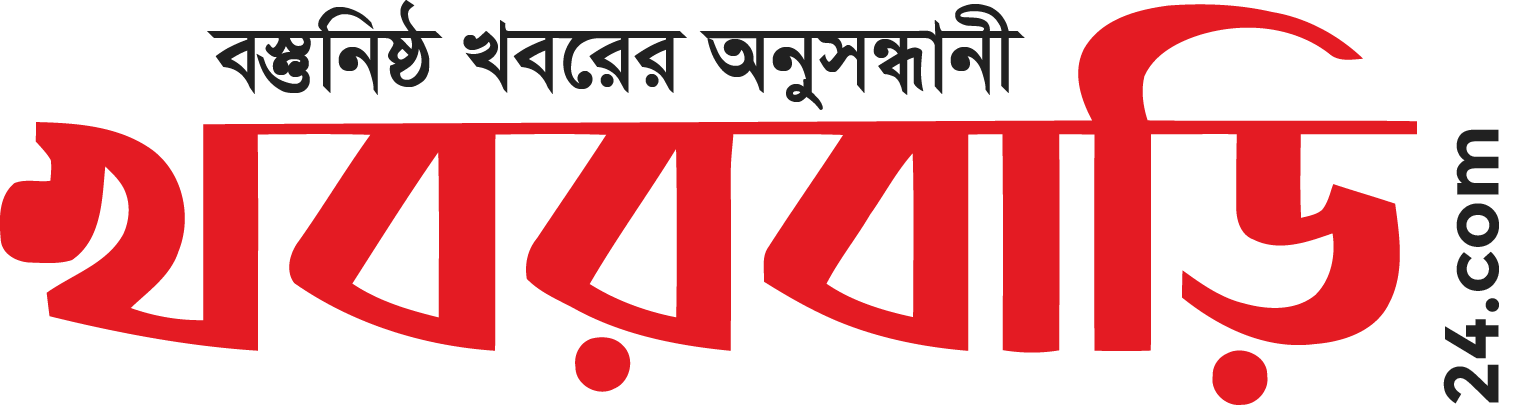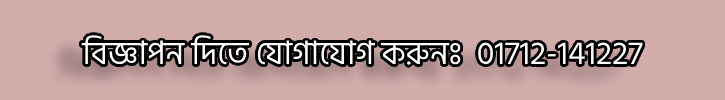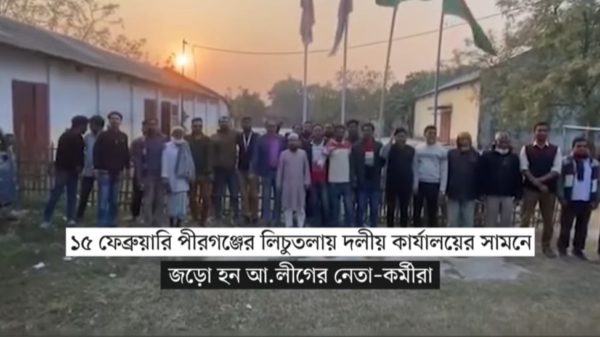পীরগঞ্জে বট–অশ্বত্থ গাছের বিয়ে; লোকাচার, পুরাণ ও পরিবেশ সচেতনতার মিশ্র উৎসব
- আপডেট হয়েছে : বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ১৯৬ বার পড়া হয়েছে

সাকিব আহসান,পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁওঃ
বাংলার গ্রামীণ জনজীবনে ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার পথ নয়, সামাজিক সংহতি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রও। এরকম একটি অনন্য লোকাচার হলো বট–অশ্বত্থ গাছের “বিয়ে”। মন্ত্রোচ্চারণ, মালাবদল, সিঁদুরদান, ভোজ ও উৎসবমুখর সামাজিক আয়োজনের মাধ্যমে এই ‘গাছের গাছ বিয়ে’ একদিকে যেমন প্রাচীন শাস্ত্র–পুরাণের প্রতীকী ব্যাখ্যাকে ধারণ করে, অন্যদিকে আধুনিক যুগে পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণের বার্তাও বহন করছে।
উল্লেখিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলঃ ঐতিহাসিক উৎস কোথায়, গ্রামীণ সমাজে এর সাংস্কৃতিক-সামাজিক তাৎপর্য কী, এবং আজকের দিনে এর ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোতে পারে; এসব
ঐতিহাসিক–ধর্মীয় প্রেক্ষাপটঃ
ভারতীয় উপমহাদেশে বট ও অশ্বত্থ দু’টিই পবিত্র বৃক্ষ হিসেবে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
অশ্বত্থ (পিপল, Ficus religiosa): উপনিষদ ও গীতায় অশ্বত্থকে বিশ্বসৃষ্টির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, “উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থম্” শ্লোকটি সেই প্রমাণ। গীতায় কৃষ্ণ নিজেকে অশ্বত্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ধর্মীয় অভিধানে অশ্বত্থ বিষ্ণুর প্রতীক।
বট (Ficus benghalensis): অসংখ্য শাখা–প্রশাখা ও দীর্ঘজীবী স্বভাবের কারণে বটকে অমরত্ব, প্রাণশক্তি ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। বহু প্রবাদে এটিকে শিব বা ত্রিমূর্তির রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।
পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে—অশ্বত্থ, বট ও পলাশ যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার প্রতীক। অর্থাৎ, এই বৃক্ষসমূহ কেবল প্রাকৃতিক নয়, সরাসরি দেবত্ব ও ত্রিগুণের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ফলে, লোকবিশ্বাসে এই গাছের যুগলতাকে দেব–দেবীর দাম্পত্য প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে।
লোকবিশ্বাস ও সামাজিক অর্থঃ
গ্রামবাংলায় প্রচলিত বিশ্বাস—বট–অশ্বত্থের বিয়ে দিলে গৃহে শান্তি, বংশবৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ মেলে।
খরা বা অনাবৃষ্টির সময় অনেক জায়গায় বৃষ্টি কামনায় এই বিয়ে দেওয়ার নজির রয়েছে।
কোথাও এটি সরাসরি কৃষিজীবী সমাজের মৌসুমি প্রার্থনা।
আধুনিক সময়ে আবার অনেকে এই আচারকে বৃক্ষরক্ষা আন্দোলন বা সবুজ সংরক্ষণের প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত করছেন।
লোকধর্মে বিশ্বাস করা হয়—যেমন মানুষের সংসার গড়ে ওঠে দাম্পত্যে, তেমনি প্রকৃতির ভারসাম্যও গাছের দম্পতি হলে স্থিতিশীল হয়।
রীতি–পদ্ধতিঃ “বিয়ে” কেমন করে হয়
আঞ্চলিক ভেদাভেদ থাকলেও সাধারণত কিছু ধাপ প্রায় সর্বত্র একই—
পাত্র–পাত্রী নির্বাচনঃ কাছাকাছি জন্মানো বা ডাল–বনে মিল থাকা বট ও অশ্বত্থকে ‘বর–কনে’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
আলংকার/পোশাকঃ বটকে বর ধরে তার গায়ে ধুতি বাঁধা হয়, অশ্বত্থকে কনে ধরে শাড়ির কাপড় পরানো হয়। নিমন্ত্রণপত্র, মিষ্টিমুখ—সবই মানুষের বিয়ের মতো।
মন্ত্রোচ্চারণ–মালাবদল–সিঁদুরদান: পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন; প্রতীকী মালাবদল ও সিঁদুরদান হয়।
প্রদক্ষিণ ও শপথঃ গাছ ঘিরে প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত জনতা বৃক্ষরক্ষা ও নতুন চারা লাগানোর প্রতিজ্ঞা করেন।
ভোজ ও উৎসবঃ গান–বাদ্য, ভোজন, মিলনমেলা—সব মিলিয়ে এটি এক সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়।
নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিস্তারঃ
শুধু বাংলায় নয়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ–সহ বহু অঞ্চলে গাছ–গাছের বিয়ে দেওয়ার নথি পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদরা একে আচার–ভিত্তিক সংরক্ষণ চর্চা( রিচ্যুয়ালাইজড কনভারসেশন) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।
এই ধরনের অনুষ্ঠান গ্রামীণ সমাজে কমিউনিটি–বিল্ডিং বা সামাজিক একাত্মতার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। নারী–পুরুষ, ধনী–গরিব নির্বিশেষে সবাই অংশ নেয়; ফলে এটি এক সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সম্প্রীতির উৎসব।
শাস্ত্র–পুরাণের প্রতীকী ব্যাখ্যাঃ
অশ্বত্থ/পিপল: বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভ করেছিলেন যে বৃক্ষতলে, সেটিই অশ্বত্থ। ফলে এর সঙ্গে জ্ঞান, মুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক যুক্ত।
বট: দীর্ঘজীবী ও ছায়াদানকারী বটকে উর্বরতা ও জীবনের প্রতীক ধরা হয়। বিবাহিতা নারীরা স্বামীর দীর্ঘায়ুর কামনায় বটপূজা করেন।
ত্রিমূর্তি–সংযোগঃ বট–অশ্বত্থ–পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষকে যথাক্রমে ব্রহ্মা–বিষ্ণু–শিবের রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ফলে এই বিয়ে কেবল বৃক্ষ–সংস্কৃতি নয়, ত্রিগুণ–সম্বন্ধীয় পুরাণকথার প্রতীকী প্রতিফলনও।
আধুনিক পুনর্নির্মাণঃ পরিবেশ ও গণসংস্কৃতি
সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে বারবার দেখা যাচ্ছে—
বৃষ্টির প্রার্থনাঃ খরাপ্রবণ এলাকায় গাছের বিয়ে বৃষ্টির কামনায় আয়োজিত হচ্ছে।
পরিবেশ প্রচারণাঃ শহর–গ্রামে সবুজ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি এই আচারকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
গণসংস্কৃতিঃ ছাপানো কার্ড, বড় আকারের নিমন্ত্রণ, গান–বাদ্য—সব মিলিয়ে এটি এক আধুনিক সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপ নিচ্ছে।
ফলে এটি আর নিছক লোকবিশ্বাস নয়, বরং সমসাময়িক পরিবেশ–আন্দোলনের প্রতীকী রূপ হয়ে উঠছে।
পীরগঞ্জ উপজেলার ৮নং দৌলতপুর ইউনিয়নের জনৈক পুরোহিত গণেশ্বর চক্রবর্তীর ভাষ্যমতে,পিতা–পুরুষের সময় থেকে এই আচার চলে আসছে। তখনকার দিনে এটা ছিল ভক্তি আর দেবতার আশীর্বাদ কামনার উপায়। এখনকার দিনে মানুষ এটাকে বৃক্ষরক্ষার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করছে। তবে আধুনিক জীবনের তাড়াহুড়ো, শহুরে দৃষ্টিভঙ্গি—এসবের কারণে হয়তো ভবিষ্যতে এই চর্চা ম্লান হতে পারে।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ
চ্যালেঞ্জ: নগরায়ন, ধর্মীয় অনীহা, তরুণ প্রজন্মের অনাগ্রহ—এসবের কারণে ভবিষ্যতে এই চর্চা হারিয়ে যেতে পারে।
সম্ভাবনা: পরিবেশ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে এটি নতুনভাবে বিকশিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি এই লোকাচারকে পরিবেশ–শিক্ষার অংশ করে তোলে, তবে এটি প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।
বট–অশ্বত্থ গাছের বিয়ে নিছক এক ‘অদ্ভুত’ প্রথা নয়। এর ভেতরে জড়িয়ে আছে—
শাস্ত্র–পুরাণের প্রতীকী ঐতিহ্য,
লোকবিশ্বাস ও সামাজিক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা,
গ্রামীণ জীবনের উৎসবমুখর সংহতি,
এবং সমসাময়িক পরিবেশ–রাজনীতির বার্তা।
অতএব, এই আচার একদিকে যেমন আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার স্মারক, তেমনি আজকের পরিবেশ–সচেতনতার প্রতীকী ভাষাও। সমাজ যদি এটিকে কেবল কুসংস্কার না ভেবে “সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ–কৌশল” হিসেবে গ্রহণ করে, তবে ভবিষ্যতেও এই চর্চা নতুন অর্থে বেঁচে থাকবে।